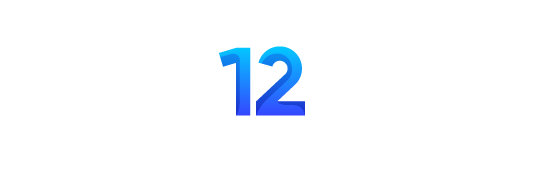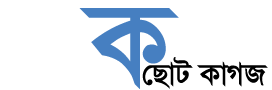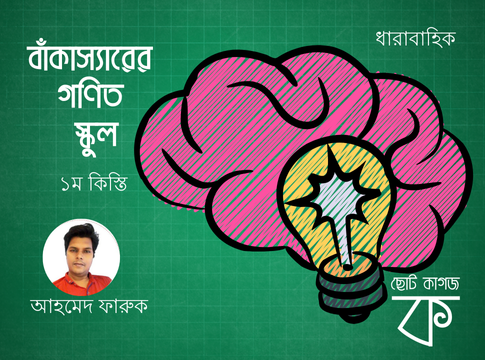আহমেদ ফারুক
—————
পর্ব ১
—————
বাঁকা স্যারের স্টাইলটা কাজী নজরুলের মতো। মাখাভর্তি কোকড়ানো চুল। সেই চুলে চুপচুপা করে তেল দেন। একটু পর পর মাখা চুলকিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবেন। বাহ্যিকভাবে একেবারেই গোবেচারা টাইপ মানুষ। পলাশপুর স্কুলের গণিতের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক তিনি। স্কুলের সবাই তাকে জীবন্ত ক্যালকুলেটর বলে। হালকালে কেউ কেউ তাকে ল্যাপটপ বলেও ডাকে।
বাঁকা স্যার বিয়ে করেননি। বিয়ে করে মানুষ কেন সময় নষ্ট করে এই বিষয়টা তিনি ভেবে পান না। বেঁটেখাটো এই মানুষটা থাকেন ধলেশ্বরী নদীর পাশে ছোট্ট একটা ঘরে। স্কুলের অন্য স্যারেরা যখন কোচিং-প্রাইভেট পড়ানোর নামে টাকার গন্ধে সারাদিন ব্যস্ত, তখন তিনি নদীর ধারে বসে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মাঝে মাঝে রাত হয়ে যায়। তিনি বসেই থাকেন। সাথে তিনি কলম আর খাতা রাখেন। সেখানে তিনি গণিতের মজার সূত্রগুলো লেখেন। গণিতের মতো এমন একটা মজার বিষয় কেন শিক্ষার্থীরা ভয় পায় এটাই তিনি ভেবে পান না।
আজো তিনি বসে ছিলেন ধলেশ্বরী নদীর ধারে। সন্ধ্যার একটু পর অপূর্ব অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিক। আজ অমাবস্যা। টুস করে চারদিকে নেমে এলো অন্ধকার। এই জায়গাটা এই কারণে বাঁকা স্যারের খুবই পছন্দ। এখনো এই এলাকায় বিদ্যুৎ আসেনি। সন্ধ্যার পর অদ্ভূত অন্ধকারে ডুবে যায় চারদিক। শুধু নদীর দুলতে থাকা এলোমেলো ঢেউগুলো অদ্ভুত রূপালি আভা ছড়াতে থাকে।
‘কি এত ভাবেন?’
অন্ধকারে চমকে ওঠেন বাঁকা স্যার। তার পেছনে শেফালী দাঁড়িয়ে আছে। এই মেয়েটা সাপের মতো নিঃশব্দে চলাফেরা করে। তিনি বললেন, ‘কি ব্যাপার তুমি?’
‘আপনারে খুঁজতে খুঁজতে চইলা আইলাম।’
‘ভালো করেছ?’
‘এই অন্ধকারে একলা একলা বইস্যা কি ভাবেন?’
‘অংক নিয়ে ভাবি?’
‘অংক নিয়ে ভাবাভাবির কি আছে? যোগ বিয়োগ করতে পারলেই হইলো।’
বাঁকা স্যার অবাক হয়ে তাকালেন। অন্ধকারে তিনি শেফালীর মুখ সেভাবে দেখতে পেলেন না। তবে সে যে হাসি হাসি মুখে উত্তরের অপেক্ষা করছে এটা বুঝতে পারলেন। অবশ্য শেফালী সারাদিনই হাসে। এত হাসি তার কোত্থেকে আসে তা তিনি ভেবে পান না। শেফালী বলল, ‘কি হইলো উত্তর মিলাইতে পারতাছেন না?’
‘একটু ভাবছি। মানে যাকে তুমি খুব সাধারণ প্রশ্ন ভাবছ তা কিন্তু সাধারণ না। গণিত কিন্তু হেসে উড়ে দেয়ার জিনিস না। যদিও গণিতের শুরু কবে ও কোথায় হয়েছিল এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। অনেকের মতে গণিতের আদিভূমি মিশর। মিশর মানে পিরামিডের দেশ। বুঝছ?’
‘ওরা তো শুনছি বড় বড় পিরামিড বানাইছে। পাথরের ওপর পাথর বসায়ে পৃথিবীর সপ্তাশ্চার্যের একটা বানাইছে। আর পাথর বসাতে তো হিসেবের ব্যাপার স্যাপার আছেই। ওই কারণেই ওরা গণিত বানাইছে।’
বাঁকা স্যার কিছুটা বিস্মিত। এই মেয়ের কথায় যুক্তি আছে। যদিও তার যুত্তিতে কোনো সত্যতা নেই। কারণ গণিতের ইতিহাস নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে। এর কারণ ভারতবর্ষে, ব্যাবিলনে এবং চিনে প্রাচীনকালে যে উন্নতমানের গণিতচর্চা হতো তার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই অনেক পণ্ডিতের মতে ভারতবর্ষই গণিতশাস্ত্রের উৎপত্তিস্থল। এমন দাবী করার পিছনে যুক্তি কী? কারণ ইতিহাসেরও একটা ইতিহাস থাকে। সেভাবে ইতিহাসের খোঁজ করলে পিছাতে পিছাতে হয়তো মানবসভ্যতার উষালগ্নে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। তবে বলা যতটা সহজ বাস্তবে তা নয়। বরং অত্যন্ত কঠিন কাজ। যত অতীতে যাওয়া যাবে তত প্রাচীন নিদর্শন এবং সাক্ষ্য প্রমাণ কমতে থাকবে। ফলে এক সময় থেমে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। সেভাবে থেমে গেছে ভারতীয় সভ্যতার অতীত ইতিহাস। সিন্ধু সভ্যতার আগের ইতিহাস আমাদের অজানা। কিংবা তার আগে কোনো সভ্যতা ছিল তা কেউ জানে না। আদৌ সভ্যতা ছিল কিনা সেও এক প্রশ্ন। তাই আমাদের শুরু করতে হবে সিন্ধু উপত্যকায় যে সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল সেখান থেকে। কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে জানা গেছে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল সাতটি স্তরে। প্রথমটির বয়স খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০০-৩২০০ অব্দের। এর চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০-১৭০০ অব্দের মধ্যে।
বাঁকা স্যার শেফালীর দিকে তাকালেন। বললেন, ‘মানুষের চিন্তা ভাবনা এতই দ্রুত ঘটে যে তা বিশাল এক প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে দেয়। কিন্তু ওই দূর আকাশের দিকে তাকাও। দেখ অসংখ্য তারায় ঢেকে আছে আকাশ। এসব তারা আল্লাহ এমনি এমনি সৃষ্টি করেননি? প্রতিটা তারা গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে রয়েছে গণিতের সূত্র। এই বিশ্বভ্রম্মাণ্ডের এই গণিতের অদ্ভূত রহস্য কে উৎঘাটন করবে? আধৌ কি তা সম্ভব?’
শেফালী জানে বাঁকা স্যার কিছু পাগল। শুধু সে না। এই এলাকার কেউ তাকে ঘাটায় না। বাঁকা স্যারের জগৎটা একেবারে আলাদা। যে জগতের সাথে অন্য কোনো মানুষের মিল নেই। জগৎ সংসার তাকে একেবারেই টানে না। সারাদিন অন্য কোনো দুনিয়ার ভাবনায় ডুবে থাকে। তবে মানুষটা অংকের জাহাজ। আর শেফালীরও গণিত নিয়ে অনেক আগ্রহ। যদিও প্রাইমারী স্কুল পাশ দিয়ে হাই স্কুলে ওঠার সাথে সাথে তার পড়াশোনার পাঠ চুকে যায়। তার নিরক্ষর বাবা তাকে জোর করে বিয়ে দেয়। ছেলে সৌদি আরব থাকে। আরবে খেঁজুর গাছের তলে বসে বসে উটের দুধ বেঁচে। এক কেজি দুই রিয়েল।
এসব ভাবতে ভাবতে নিজে নিজেই হেসে ওঠে শেফালী। তার হাসিতে ফিরে তাকায় বাঁকা স্যার। কিছু বলে না। এই মেয়ে এমনি এমনি হাসে কেন? হাসির কি কোনো গাণিতিক সূত্র আছে?
অবশ্য বাঁকা স্যার এখন ভাবছেন অন্য বিষয়। চীনা গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস নিয়ে। এই ইতিহাস অতি প্রাচীন। রোশিও মিকামির মতে ২৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেদেশে গণিতচর্চার রেওয়াজ ছিল। তবে তা বিক্ষিপ্তভাবে। পদ্ধতিগতভাবে গণিতচর্চার ভাবনা চিনাদের মধ্যে শুরু হয়েছিল ২৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পীত সম্রাট হুয়ান তি’র আমলে। তবে তা পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে অনেক সময় লেগেছিল। ১৫২ খ্রিস্টপূর্বে চাঙ্গ সাঙ্গ নামে একজন চিনা গণিতবিদ ‘কিউ চাঙ্গ সুয়ান সু’ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অনেকের মতে পদ্ধতিগতভাবে লেখা এটাই চিনাদের প্রথম গণিতের বই। এর আগে অবশ্য আরো একটি পদ্ধতিগত বই লেখার চেষ্টা হয়েছিল। বইটির নাম ‘আই কিং’। দ্বাদশ খ্রিস্টপূর্বে চিনা পণ্ডিত ওয়ান ওয়াঙ্গ-এর লেখা এই বইটি মূলত বিজ্ঞানের। এতে গণিতের কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই একে পূর্ণাঙ্গ গণিতের বই বলা চলে না। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে প্রাচীনকালে ভারতীয়রা গণিতকে যে ভাবে দেখতেন চিনারা সেভাবে দেখতেন না। তাঁদের কাছে গণিত ছিল মূলত ব্যবহারিক ও বাস্তব সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার মাত্র। তাই তাঁদের কাছে গণিত ভারতীয়দের মতো সর্ববিদ্যার ঊর্ধ্বে ছিল না।
গ্রিক গণিতের ইতিহাস অত পুরোনো নয়। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর আগে গণিতের আঙিনায় গ্রিকদের তেমন দেখা যেত না। এর প্রায় দু’হাজার বছর আগে থেকে মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় ও প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতরা গণিত চর্চায় আত্মনিযোগ করে আসছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে গ্রিকদের পূর্বে কোনো জাতিই গণিতের নিয়মের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করেন নি। গ্রিক জাতিরাই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে গণিতের কতকগুলি বিক্ষিপ্ত তথ্য আবিষ্কারই যথেষ্ট নয়। এর নেপথ্যে যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা ক্রিয়াশীল তার রহস্যভেদই গবেষণার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাই দেরিতে শুরু হলেও গ্রিক গণিতচর্চার ধারা এক নতুন পথের সন্ধান দেয়।
মিশরে গণিতের উদ্ভব কবে হয়েছিল তার সঠিক সময় জানা সম্ভব নয়। প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণার উপর নির্ভর করে তাঁদের গাণিতিক জ্ঞান কেমন ছিল সে সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে আইসেনলোর ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত মিশরীয়দের একটি প্রাচীন গণিত গ্রন্থ ‘আহমেস্ প্যাপিরাস্’ পাওয়া যায়। তবে এটি মূল গ্রন্থ নয়। আনুমানিক ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরে হিকোসাস রাজত্বকালে ফারাও আ-আসার রে’র সময় আহমেস্ নামে জনৈক ব্যক্তি পূর্বের কোনো গ্রন্থ বা প্যাপিরাস থেকে সঙ্কলন করেছেন। পণ্ডিতদের অনুমান মূল গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ১৮৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৮০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে। মিশরে তখন তৃতীয় আমেন এম হেটের রাজত্বকাল। তবে এই সময়কাল নিয়ে সব পণ্ডিত এক মত নন। বার্চ সাহেবের মতে এর রচনা কাল ৩৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
ব্যাবিলনে কোনো কিছু লিখে রাখার জন্য মাটির চাকতি ব্যবহার করা হতো। মাটির চাকতি যখন নরম থাকত তখন সরু শলাকার সাহায্যে লেখা হতো। তারপর তা শুকিয়ে পোড়ানো হতো যাতে সেগুলি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। এগুলিই ছিল ব্যাবিলনীয় গ্রন্থ। খননকার্য চালিয়ে অসুরবনিপালের (মৃত্যু ৬২৬ খ্রিস্টপূর্ব) গ্রন্থাগারে ২২০০০ কিউনিফর্ম লিপির চাকতি পাওয়া গেছে। আর প্রায় ৫০,০০০ এই ধরনের চাকতি নিপ্পুর মন্দিরের গ্রন্থাগারে পাওয়া গেছে । বিশেষজ্ঞদের মতে এই চাকতিগুলি লেখা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ৪৫০ অব্দের মধ্যে। এই চাকতিগুলির মধ্য থেকে গণিত সংক্রান্ত যে চাকতিগুলি পাওয়া গেছে তার অস্তিত্বকাল প্রায় ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এ থেকে অনুমান করা হয় প্রাচীন ব্যাবিলন এই ৮০০ বছর গাণিতিক তৎপরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।
ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে মিশর ও ব্যাবিলনের সঙ্গে গ্রিকদের যোগসূত্র ছিল। সেই সূত্র ধরেই মিশর বা ব্যাবিলনে গিয়ে গ্রিকদের গণিত শেখা। এরপর তাঁরা নিজ দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়েতুলে মেধাবী ছাত্রদের গণিত শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশে গণিত শিক্ষার প্রসার ঘটাতে থাকেন। এ ব্যাপারে থ্যালেস-কে (Thales) গ্রিক গণিতের জনক বলা হলেও আধুনিক গণিতের সূত্রপাত হয়েছিল মূলত যে তিনজন গ্রিক গণিতবিদের হাত ধরে তাঁরা হলেন— পীথাগোরাস (৫৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ), ইউক্লিড (৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এবং আর্কিমিডিস (২২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। প্রাচীন গ্রিক গণিতের ইতিহাসকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে— (১) থ্যালেস থেকে পীথাগোরাস-এর সময়কাল পর্যন্ত ক্লাসিক্যাল যুগের সূচনাপর্ব, (২) পীথাগোরাসের পরবর্তী সময় থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় ‘মিউজিয়াম’ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত ক্লাসিক্যাল যুগ এবং (৩) আর আলেকজান্দ্রিয় যুগ হলো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরবর্তী সময় অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত।
প্রাচীনকালে গণিতচর্চায় রোমকদের তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। ব্যবহারিক জীবনে যতটুকু গণিতের প্রয়োজন তার বাইরে গণিত শিক্ষার কোনো প্রয়োজন আছে বলে তাঁরা মনে করতেন না। তাই গণিত গবেষণায় রোমকদের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। একমাত্র বোয়েথিয়াস্ ছাড়া প্রাচীন রোমক ইতিহাসে আর কোনো গণিতবিদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও গাণিতিক গবেষণায় গ্রিক গণিতজ্ঞদের মতো তাঁর কোনো মৌলিক অবদান নেই। তাই তাঁকে সমকালীন গ্রিক গণিতবিদদের সঙ্গে সম আসনে বসানো যায় না।
জ্ঞান বিজ্ঞানে আরব জাতির অবদান লক্ষণীয়। পীথাগোরাস, ইউক্লিড বা আর্কিমিডিসের মতো গণিতজ্ঞ আরবে জন্মান নি ঠিকই তবে আল্-খোয়ারিজ্মি, আল-বাত্তানি ও ওমর খৈয়ামের প্রচেষ্টায় সেখানে গণিতের যে অভাবনীয় উন্নতি সাধন হয়েছিল তা বিস্ময়কর। বিশেষ করে বীজগণিতে আরব গণিতজ্ঞদের অবদান প্রশংসনীয়। ত্রিকোণমিতি ও বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতিতেও তাঁরা আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন।
গ্রিকদের গণিত শিক্ষা যেমন মিশরীয়দের কাছ থেকে তেমন আরবদের গণিত শিক্ষা মূলত মেসোপটেমিয়া ও ভারত থেকে। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরব পণ্ডিতরা একটি চিরস্মরণীয় কাজ করে গেছেন। তাঁরা ভারতীয় ও গ্রিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অমূল্য গ্রন্থরাজি নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। শুধু অনুবাদ করেই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি। মৌলিক গবেষণার দ্বারা গণিতের আঙিনায় তাঁরা তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন। ব্রহ্মগুপ্তর লেখা ‘ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্তের’ খ্যাতি স্বদেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রন্থটি পারসী ভাষায় অনুদিত হওয়ার পর থেকে। খলিফা আল্-মানসুরের রাজত্বকালে ইব্রাহিম আল্-ফাজারি ও ইয়াকুব ইব্ন্ তারিক নামে দুই আরব্য গণিতজ্ঞ এটি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এরপর থেকেই আরবে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। গ্রন্থটির আরবী নাম রাখা হয়েছিল ‘সিন্দহিন্দ’। ব্রহ্মগুপ্তের ‘খণ্ডখাদ্যক’ গ্রন্থটি ‘অর্কন্দ’ নামে আরবীতে অনুদিত হয়েছিল।
ভারতবর্ষে গাণিতিক চিন্তার সূচনা কবে হয়েছিল তা বলা কঠিন। তবে বৈদিক যুগে গণিতের বিশেষ করে সংখ্যা সম্বন্ধীয় গণনার ধারণা ছিল। বেদের বিভিন্ন অধ্যায়ে এর নিদর্শন রয়েছে। তবে আলাদা করে গণিতের কোনো গ্রন্থ এ যুগে পাওয়া যায় নি। তাই অনুমান করা যায় এই সময় যে গণিতচর্চা হত তা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। তাহলে কি ধরে নেয়া যেতে পারে যে বৈদিক যুগের আগে ভারতবর্ষে গণিতের কোনো চর্চা হতো না? সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত এমনই ধারণা ছিল। মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা ও চানহূদড়োর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের পর এই ধারণা পাল্টে যায়। নগর পরিকল্পনা ও ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে সে যুগে পর্যাপ্ত গণিতচর্চা হতো। যদিও প্রামাণিক কোনো প্রন্থ ধ্বংসাবশেষের ভিতর থেকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। পাঁচ হাজার বছর আগে স্থাপিত কোনো নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে যখন অসংখ্য মূর্তি, ছবি, চিত্রিত মৃৎপাত্র, শীলমোহর, স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া যায় তখন অস্বীকার করার উপায় নেই যে সে যুগে ললিতকলার পর্যাপ্ত চর্চা ছিল।
মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা ও চানহূদড়োর ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে ছোট বড় নানাধরনের বাটখারার মতো জিনিস। এগুলি যে পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হতো সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এছাড়াও পাওয়া গেছে ভাঙা দাঁড়িপাল্লা, বিভিন্ন দাগকাটা স্কেল বা মাপনী যা ব্যবহার করা হতো মাপজোকের কাজে। গুজরাটের বলস্কান্ত জেলার দত্রানা থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে সান্ত্রালিতে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন আমলের একটি কারখানা। এখানে তৈরি হত নানা ধরনের ফলা, খাঁজকাটা যন্ত্র যা সব ছিল বর্গ ষঙতলাকৃতির (Square parallelopiped)। পণ্ডিতদের ধারণা এই কারখানাটি সিন্ধু সভ্যতা আমলের। সিন্ধু সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল ব্রোঞ্জ যুগে। এই ভগ্নাবশেষ থেকে পাওয়া নিদর্শনগুলি সবই ছিল তামার তৈরি।
হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর নগর পরিকল্পনা ছিল দেখার মতো। সেখানকার সমস্ত রাস্তাই ছিল চওড়া ও সোজা। ছিল উন্নতমানের পয়ঃপ্রণালী। বাড়িগুলি ছিল পোড়া ইটের তৈরি। প্রত্যেকটি ইটের আকৃতি ছিল কোনো না কোনো জ্যামিতির আকার বিশিষ্ট— কোনোটা কীলকাকৃতির, কোনোটা বা চতুস্তলাকৃতির, কোনোটা সমকোণী ত্রিভুজাকৃতির আবার কোনোটা পিরামিডাকৃতির। মহেঞ্জোদড়োর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সাগরের কাছে লোদালে যে বিশাল ডক্ইয়ার্ডের সন্ধান পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় যে সে যুগে নৌ-বিদ্যা এবং নৌ-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। জ্যামিতি বা গণিতবিদ্যা ও জরিপবিদ্যার সুগভীর জ্ঞান না থাকলে এসব সম্ভব হত না। তাই একথা মনে করা অসঙ্গত হবে না যে প্রাচীন ভারতের গণিত চিন্তার শুরু সেই প্রাক্ বৈদিক ভারতীয় সভ্যতার সময় থেকেই।
এখন প্রশ্ন হল, সিন্ধু সভ্যতার আগে ভারতভূমি কি মনুষ্য বর্জিত ছিল? কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে সিন্ধু সভ্যতা দ্রাবিড় সভ্যতারই একটি রূপ। এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল ব্রোঞ্জ যুগে (Bronze Age)। এই যুগ তাম্র যুগেরই একটি পরিণত রূপ। এর উদ্ভব সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময় থেকে। সিন্ধু সভ্যতায় তামা এবং ব্রোঞ্জ নির্মিত হাতিয়ার ও তৈজসপত্র ইত্যাদির নিদর্শন পাওয়া গেছে। ব্রোঞ্জ একটি সংকর ধাতু। তাই বলা যায় তাম্র যুগের শেষ লগ্নের মানুষেরা এই সংকর ধাতু নির্মাণের কলাকৌশল করায়ত্ত করতে পেরেছিল। যেকোনো বিজ্ঞানের পিছনে গণিতের প্রয়োগ থাকে। সেটা প্রত্যক্ষও হতে পারে বা পরোক্ষও হতে পারে। গণিত ছাড়া কোনো বিজ্ঞান এগোতে পারে না। এখন দেখা যাক ভারতভূমিতে মানুষের পদচিহ্ন পড়েছিল কোন সময়ে— ব্রোঞ্জ যুগে না আরো আগে? ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে প্রত্নপ্রস্তর যুগের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা সম্ভবত এই যুগের মানুষেরই বংশধর। দক্ষিণভারত, বিন্ধ্যপর্বত এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকদের মতে কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীরা সম্ভবত এই যুগের মানুষেরই বংশধর। তাহলে বলা যায় ব্রোঞ্জ যুগের আগেও ভারতের মাটিতে মানুষের বসবাস ছিল। তবে নগর সভ্যতার সূচনা সম্ভবত ব্রোঞ্জ তথা সিন্ধু সভ্যতাতেই। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের অর্থাৎ দ্রাবিড়দের আগমন বহির্ভারত থেকে। এমন ধারণার কারণ দ্রাবিড়দের ভাষা এবং বেলুচিস্তানের ইস্লাম ধর্মাবলম্বী ‘ব্রাহুই’ জাতির লোকেদের ভাষায় অনেক মিল আছে। যদি ধরে নেয়া হয় যে আর্যদের মতো সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরাও বহিরাগত ছিল তাহলে প্রশ্ন হতে পারে এরা কি খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০-৩৩০০ অব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে এদেশে এসেছিল, না আরো আগে থেকেই এদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল? ব্রোঞ্জ প্রযুক্তি যদি এদের সঙ্গেই এসে থাকে তাহলে ধরে নেয়া যায় এদেশে বিজ্ঞান ও গণিতের আগমনও এদেরই হাত ধরে। প্রসঙ্গত বলা যায় মেসোপটেমিয়ার সুমেরীয় সভ্যতা এবং নীল নদের উপত্যকায় গড়ে ওঠা মিশরীয় সভ্যতার বিকাশও প্রায় একই সময়ে। ঐতিহাসিকদের মতে এই সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের মতো সময়ে। সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার যোগাযোগ থাকলেও মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল কিনা জানা নেই। তাই ধরে নেয়া যেতে পারে যে ভারতীয় গণিতের বিকাশ এদেশের মানুষের চিন্তা ভাবনাতেই ঘটেছিল। তাই যাঁরা মনে করেন ভারতবর্ষই গণিতের সূতিকাগার তাঁদের ভাবনাকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। এনিয়ে অবশ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে ভারতীয় গণিত যে মিশর, ব্যাবিলন বা চিনের থেকে পিছিয়ে ছিল না সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।
শেফালী ধাক্কা দেয় বাঁকা স্যারকে। কিন্তু বাঁকা স্যারের যেন কোনো হুস নেই। কয়েকবার ধাক্কা দেয়ার পর অদ্ভুত একটা শব্দ করে ওঠেন। শেফালী বলে, ‘আফনার কি হয়েছে কন দেহি? ওভাবে এক ধ্যানে তাকিয়ে আছেন ক্যান?’
বাঁকা স্যার কিছুই বলে না। যেন তিনি এই জগতে নেই। কিংবা এই জগতের কোনো কিছুর সাথে তাঁর কোনো যোগসূত্রও নেই।
শেফালী লক্ষ্য করে দেখে বাঁকা স্যার অনেকক্ষণ ধরে নড়াচড়া করছেন না। যেন একটা মূর্তি। এমনকি তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে না।
শেফালী স্যারের একটু কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কানটা একটু সামনে টেনে স্যারের বুকের শব্দ শোনার চেষ্টা করে। কোনো শব্দ নেই। কয়েকবার সে ডাকে, ‘স্যার, স্যার।’ উত্তর পায় না।
কিছুটা ভয়ে শরীর জড়িয়ে আসে শেফালীর। কি হলো মানুষটার। সে আবারো জোরে জোরে ধাক্কা দেয়। এমন সময় কিছুটা চমকে ওঠে তিনি শেফালীর দিকে তাকান। তার শরীর দিয়ে ঝরঝর করে ঘাম পড়ছে। তিনি বললেন, ‘তুমি কি কিছু জিজ্ঞেস করলে?’
বাঁকা স্যার এমনভাবে কথা বলছেন যেন কিছুই হয়নি। শেফালীর ভয়টা একটু কমলো। সে আমতা আমতা করে বলল, ‘কি যেন ভাবতাছিলেন আফনে। অনেকক্ষণ ধইরা।’
‘অতি সাধারণ একটা ভাবনা। গণিতের ইতিহাসে মিশরীয়, গ্রিক, আরবীয়, মেসোপটেমিয়া, ভারতীয় আর চীনাদের অনেক অবদান আছে। কিন্তু বাঙালিদের কোনো অবদান নেই।’
‘অবদান থাকবো কি করে? পেডের চিন্তাতেই তো আমরা অস্থির। আর আমরা তো শিক্ষিত হওয়ার জইন্যে বই পড়ি, জ্ঞানের জইন্যে পড়ি না।’
‘বাহ! দারুন একটা কথা বলেছ তো। পড়তে তো হয় জ্ঞান আরোহনের জন্য।’
‘কজন আর জ্ঞান চায় কন। সবাই চায় সার্টিফিকেট। দেশের শাসক চায় পাশের হার বাড়াইতে। মানে পরিসংখ্যানে জীবন মাপে। দেখেন না এই দেশে মানুষ বই পড়ে হুজুগে। যে ভালো হুজুগ দিতে পারবো তার বই পড়বো। ভালো বই দিয়া কি হইবো? সবার দরকার চাকচিক্য।’
‘তুমি এত সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলা কবে থেকে শিখছ?’
‘আমিও অনেক পড়তে চাইছিলাম স্যার। কিন্তু কপালে আছে চুলা ঠেলা। তাই চুলা ঠেলি।’
‘তুমি চাইলে আমার কাছে পড়তে পারো। এমন না যে স্কুল কলেজে পড়েই কেবল শিক্ষিত হওয়া যায়। একটু আগে তুমি একটা দামী কথা বলেছ। সবাইকে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য পড়তে হবে। তুমি বরং তাই করো। রোজ শিখবে।’
‘আপনি শিখাইলে শিখবো।’
‘কিন্তু আমি নিজেই তো ভালো কিছু জানি না। গণিতের একেবারে তলানিতে পড়ে আছি।’
‘আপনি যতটুকু জানেন ততটুকুই আমারে শেখান।’
কথাটা বলেই শেফালী মুচকি হাসে। যদিও অন্ধকারে হাসিটা বাঁকা স্যার দেখতে পায় না। সে মনে মনে ভাবে, একজন জ্ঞানী মানুষ নিজেরে কত তুচ্ছ ভাবে।
বাঁকা স্যার বলে ওঠেন, ‘তুমি এখন থেকে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবে?’
‘ক্যান স্যার? এহন যেই ভাষায় কই সেই ভাষা কি খারাপ?’
‘ভাষা কখনো খারাপ হয় না। তবে গণিতের সম্মানে এমন করবে। তাছাড়া জ্ঞান যত বেশি নিতে পারবে তত বেশি গুছিয়ে কথা বলতে পারবে। এতে তোমার নিজের প্রতি ধারণাও পাল্টাতে থাকবে। মনে হবে আমি কিছু শিখতে পারছি।’
‘ঠিক আছে স্যার।’
‘আর হ্যাঁ নিজেকে সবসময় ছাত্র ভাববে। তাহলে শিখতে পারবে অনেক বেশি।’
‘ঠিক আসে স্যার। আপনে যেভাবে বলবেন সেভাবেই হবে। তবে এখন চলেন। টাকি মাছের ভর্তা আর লাউয়ের ভাজি করেছি। গরম গরম খাইবেন।’
‘আজ রাতে কিছু খাবে না শেফালী।’
‘খাবেন না মানে?’
‘আজ অমাবস্যা। আকাশে অনন্ত নক্ষত্রবীথি। আর আমি লক্ষ করেছি এই অনন্ত নক্ষত্রবীথির মাঝেই ফিবোনাক্কি সংখ্যার একটা গোপন সূত্র আছে।’
শেফারী ফিবোনাক্কি সংখ্যা সম্পর্কে কিছুই জানে না। ফিবোনাক্কি মানে কি কে জানে? এটা খায় না মাথায় দেয়, কে জানে। সে বলল, ‘চলেন তো রাতে না খেলে শরীর অসুস্থ হবে।’
শেফালী বাঁকা স্যারের হাত ধরলেন। তার হাতটা অদ্ভুত রকমের ঠাণ্ডা।